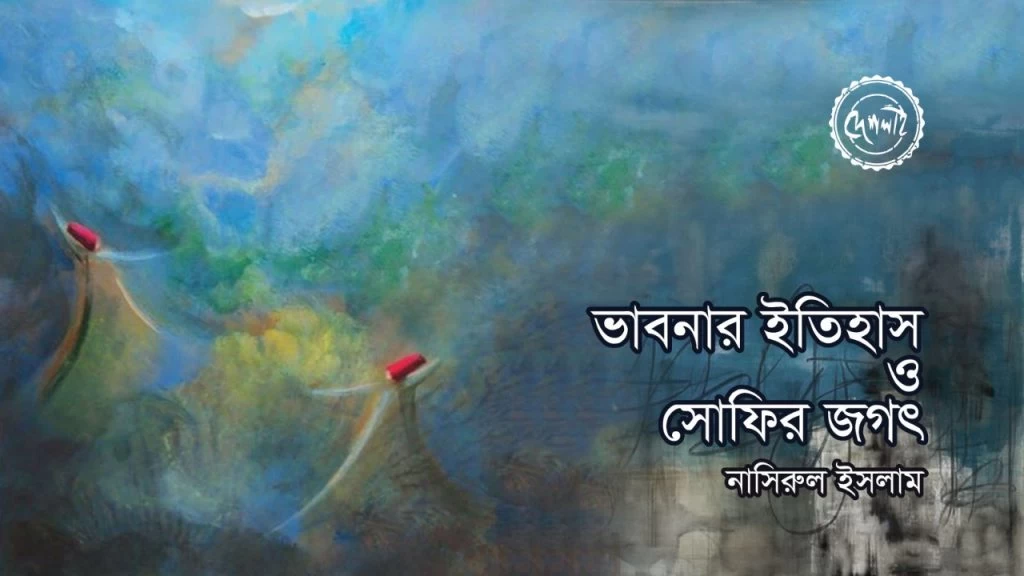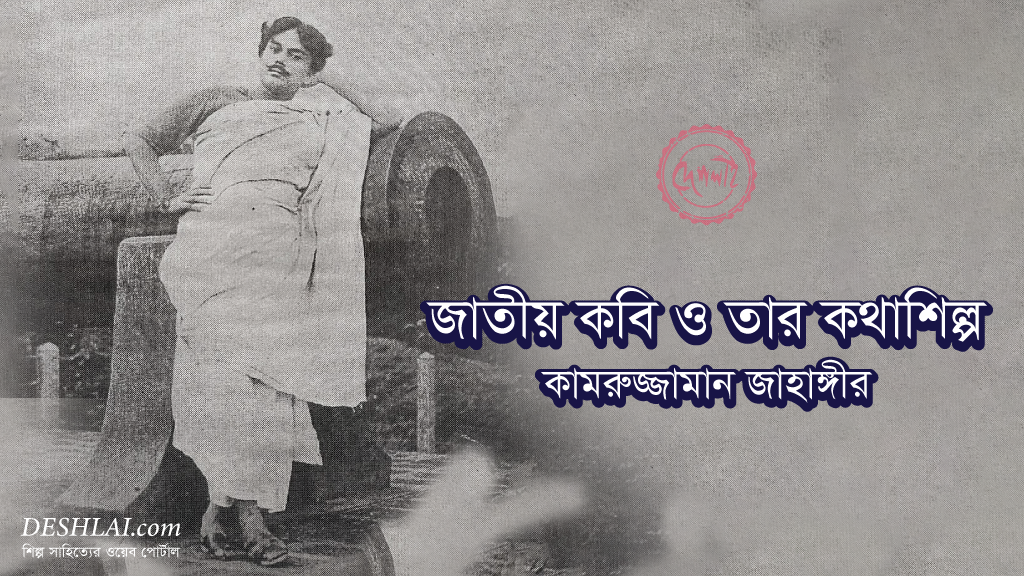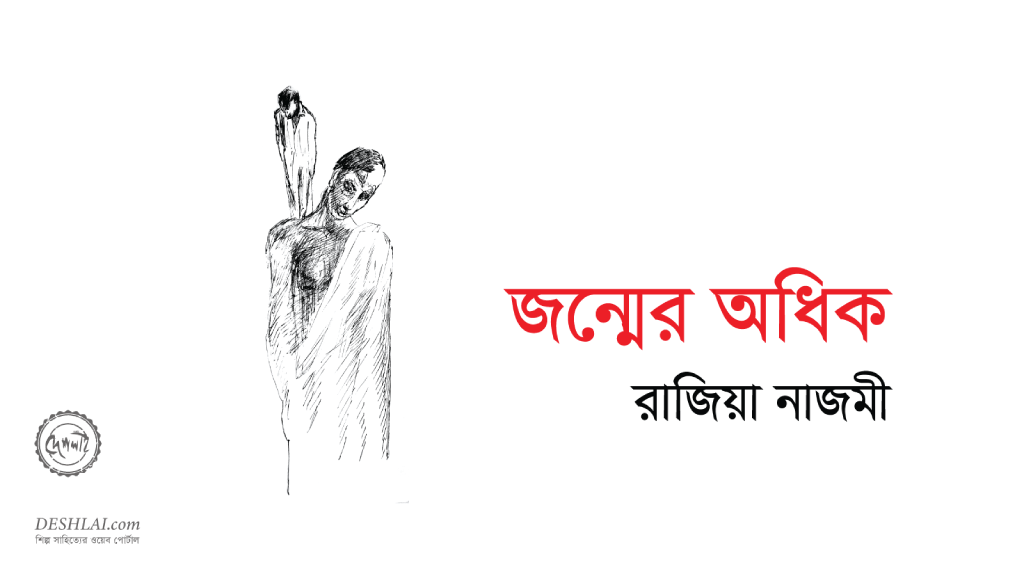১ .
ভাবনার ইতিহাস : সুদীর্ঘ অতিক্রমণ
দৈবে বিশ্বাস নেই, নইলে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মানবসভ্যতার ইতিহাসের এই সবিশেষ ব্রাহ্মক্ষণটি বোধ করি সহজেই তার দৈবত্ব দাবি করে আমাদেরকে অভিভূত করে ফেলত। খ্রি.পূ. ৬০০ অব্দ। কবি-কল্পনা হলে বর্ণনাটি এমন হতো – প্রথম উষালগ্ন, মানবসভ্যতার মননের ইতিহাসের কেবল-উঠি-কোমল সূর্যখানা তার টলমলে আলো ফেলে প্রথম পূত আঁচড় কেটে গেল মাটিতে, পথিক হবার প্রথম মন্ত্র তার কণ্ঠে – কী পূর্বে, কী পশ্চিমে; পুরনো বিশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে মানুষ এক সুদীর্ঘ আত্মজিজ্ঞাসার পথে। এদিকে ভারতবর্ষে বুদ্ধ, মহাবীর মঙ্খলীপুত্ত, রামজীবক, চীনে কনফুসিয়াস, লাওৎসে, পারস্যে জরাথ্রুষ্ট, গ্রিসের সামোস দ্বীপে পিথাগোরাস, মিলেটাসে থেলিস, অ্যানাক্সিমেনিস – এ কি কোনো দৈব? নাকি সামাজিক প্রেষণা? যার গভীর থেকে মানবসভ্যতা পা বাড়িয়েছিল এক সুকঠিন আত্মজিজ্ঞাসার পথে। এ-কথা অ-প্রমাণের আর কোনো উপায়ই আমাদের হাতে নেই যে মানবসভ্যতা তার মননের পথের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় যে দুর্লভ অর্জন ঘরে তুলেছে, তার পুুরোটাই তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার গর্ভ থেকে জাত।
ভারতবর্ষে তখন বৈদিক যুগের শেষাশেষি। প্রথম বৈদিক যুগের সেই উদার মানবতামুখী সমাজের রুগ্ণ ক্ষীণপ্রাণ-দশা। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের পশুপালন থেকে কৃষিতে উত্তরণ ঘটেছে। তার হাতে এসেছে উদ্বৃত্ত সম্পদ। শ্রম-বিভাজনের তাগিদে সমাজের পেশা-বিভাজন মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে ভয়ানক শ্রেণী-বিভাজন হিসাবে, অর্থনৈতিক স্বার্থে। আর্যদের চল ঘটানো নানান যোগ, যার সাথে মানুষের প্রাণের সংশ্রব ছিল একদিন, সেগুলো ক্রমশ চরম আচারনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিকভাবে দীন মানুষেরা অতিশয় ব্রাত্যজন হিসাবে সমাজের একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সেই কঠিন শাস্ত্রাচার-জীর্ণ সমাজে একজন বুদ্ধ বেড়ে উঠলেন। তিনি ভারতবর্ষে মানুষকে বড়ো করে তুললেন।
অন্যদিকে, ঈজিয়ান সাগরের মানসকন্যা – গ্রিসের তখন সবে সকালের ঘুম-ভাঙা-আলস্য কাটতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের মনে দীর্ঘকাল যে জিজ্ঞাসাগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল, সমাজের অন্তর্গত প্রেষণা – সে-সকল প্রশ্নকেই জাগিয়ে তুলছে। যে-আইন সমাজে পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে, সে-আইন যে কী, তা মানুষ জানতে চায়। একদিকে অভিজাত শ্রেণী চিরাচরিত নিয়মানুসারে পুরনো ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার চেষ্টায় তৎপর। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। আমরা জানি, এ দুইয়ের দ্ব›দ্ব থেকেই ‘টাইরান্ট’ (tyrant) সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। কারণ সাধারণ জনগণ তখন বিদ্রোহী; কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা নেয়ার জন্য অপ্রস্তুত। ফলে, যেখানেই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একজন পারিবারিক অন্তর্কোন্দলে বিমুখ হয়ে সাধারণ জনগণকে সাহায্য করে জয়ী করে তুলল, তখন দেখা গেল, অপ্রস্তুত জনগণ তাকেই রাজা বলে মানল। এভাবেই পুরনো নিয়মের বাইরে এসে যারা রাজা হলো তাদেরই নাম দেয়া হয়েছিল টাইরান্ট। গ্রিসের অনেক নগর-রাষ্ট্রেই তখন টাইরান্টদের রাজত্ব চলছে। গ্রিক উপনিবেশ মিলেটাসের তখন দারুণ টালমাটাল অবস্থা। বিক্ষুব্ধ জনগণ অভিজাতদের স্ত্রী-পুত্রদের হত্যা করে বসল। অভিজাতরা তাদের বিরোধীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারল। এমন নাভিশ্বাস সামাজিক অবস্থায় মানুষ নতুন করে ভাবতে বসল। এতদিন যা কিছু তার জিজ্ঞাসা, তার সবকিছুর সহজ সমাধান খুঁজে নিত পুরাণ থেকে। কিন্তু এখন পুরাণের বাইরে এসে মানুষের নতুন জিজ্ঞাসা তৈরি হল। দীর্ঘদিনের পুরাণাশ্রিত বিশ্বাস যেন তাকে আর তৃপ্ত করতে পারছে না। সেই শুরু হলো পুরাণের বাইরে এসে মানুষের জিজ্ঞাসা। অভিনব তার উদ্ভাবনা, সুদীর্ঘ তার পথ। মানুষের বিস্ময়ের কাছে যখনই কোনো নতুন ভাবনা এসে প্রণাম ঠুকেছে, তখনই, যারা বিস্মিত হতে জানে, পরম আহ্লাদে তাকে আপন করেও নিয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, মানবসভ্যতার ইতিহাস অন্তত সেই সাক্ষ্যই দেয়, সে-সকল ভাবনার যথাবস্তুকে হারিয়ে তার অসাড় কঙ্কাল আঁকড়ে মানুষ পুরনো অভ্যাসে তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছে। এই সময়টা ছিল অন্যরকম, বাইরের আন্দোলন এসে এতদিনের ঘুম-পাড়িয়ে-রাখা বিবশ জিজ্ঞাসাগুলোকে যখন জাগিয়ে তুলল, তখন, পুরনো অভ্যাসবশত পুরাণের সেই মনোমুগ্ধকর বিশ্বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে তারা অনুভব করল, আগের মতো তাদের দৃষ্টি যেন জুড়োচ্ছে না। কী এক অতৃপ্তি আচ্ছন্ন করে আছে। সেই থেকেই মানুষের ভাবনার ইতিহাস। সেই থেকে দর্শনের যাত্রা শুরু।
২.
বহুবর্ণ পথের গল্প
এ হচ্ছে নানাযোগে বহুবর্ণ এক পথের গল্প। যার সত্যিকারের শুরু আর শেষ মানুষের অজানা। কিন্তু যে জায়গা থেকে পথিক প্রথম হাঁটতে শুরু করল, সেই তার সত্যিকারের পথ হয়ে ওঠার শুরু, সেই তার ইতিহাস। সে-পথ বয়ে চলেছে আপন তাগিদে। কিন্তু সে তাগিদ অন্তরে যত সত্য হয়েই বাজুক না কেন, বাইরে তার রূপ ভিন্ন, অন্তত ভিন্ন হতে বাধ্য। কোথায়ও সে মুখিয়ে উঠেছে, কোথায়ও সে ড্যাব ড্যাব চোখে বিস্ময়ভরা বালকের মতো বিহ্বলতায় দাঁড়িয়ে। কোন্ দূর থেকে মানুষেরা এসে তাকে বলল, দাঁড়া দেখি পিঠ সোজা করে, একটু আরাম করে ঘর বাঁধি; সেখানে পথ বাঁধা পড়ে গেল তার গার্হস্থ্য কাজে। তারপর কিছুদূর যেতে না-যেতেই বুড়োঠাকুরের বা বীরু রায়ের সেই প্রায়-বৃদ্ধ বটগাছটা তাকে জোর করে ঘাড় বাঁকিয়ে দিল, বলল, এবার ও-মুখো, পথ বেয়ে চলল অন্যদিকে। তারপর কয়েক পা ফেলেছে কি ফেলেনি, হাটুরের দল এসে সরগরম বসে পড়ল পসরা নিয়ে। পথের নির্জনতা ভাঙল। চলল মানুষের লেনদেন। এভাবে দু’ পাশের ঘর-বাড়ি-ভিটেমাটি-বৃক্ষের চাপে পথ হয়ে উঠল নানা রূপের, নানা রঙের, নানা ঘরের, নানা জনের। মাঝে মাঝে নিজের অন্তর্গত তাগিদে বয়ে চলা যে হয়ে ওঠেনি তা নয়, তবে সেখানেও সুদীর্ঘ বাঁশবনের ছায়া পড়ে তাকে চুপচাপ অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে।
মানুষের ভাবনার ইতিহাসটাও কখনো বিচ্ছিন্ন বা কেবল স্ব-তাগিদ উদ্ভূত নয়। সব সময়ই নানাযোগে বহুবর্ণ পথের মতো দু’পাশের ঘর-বাড়ি-ভিটেমাটি-বৃক্ষের চাপেই তার রূপ বদলেছে। খ্রি.পূ. ৬০০ সালে গ্রিসের উপনিবেশ – এশিয়া মাইনরের মিলেটাস তখন বিকাশমান বাণিজ্যিক নগর, সারা নগর তখন ক্রীতদাসে ঠাসা। ভয়াবহ শ্রেণীদ্বন্দ্ব চলছে অভিজাত শ্রেণী আর সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাল্টে যাচ্ছে মানুষের বিশ্বাস, নিজেদের চিনে নেবার পুরনো পদ্ধতি। গ্রিক উপাখ্যানে বর্ণিত সাত জ্ঞানীর এক জ্ঞানী থেলিস সময়ের একেবারে প্রথম বিন্দুতে গিয়ে প্রশ্ন তুললেন, জগৎ সৃষ্টির মৌল উপাদান, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের মূল কী?
মিলেশিয়ান স্কুলের আরো যে তিন দার্শনিকের কথা আমরা জানতে পারি, তাঁদের সবারই জিজ্ঞাসা ছিল এই যে, আসলে কী সেই মৌলবস্তু যা দিয়ে জগৎ তৈরি হয়েছে? সে ভাবনা নানা পাখায় ভর করে ডেমোক্রিটাসে এসে ঠেকেছে। তারপর প্রকৃতি থেকে মানুষের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে মানুষ, সমাজে মানুষের অবস্থান, রাষ্ট্র-সম্পর্ক, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি আরো নানা বিষয়। সেক্ষেত্রেও বাইরের ঢেউ এসে উসকে দিয়েছে মানুষের এই প্রশ্নগুলো। কারণ প্রকৃতিবাদী দার্শনিকের পরেই সোফিস্টরা দখল করে বসল মানুষের ভাবনা-ইতিহাসের পরম্পরা। তাঁরা মূল গ্রিক ভূখণ্ডের মানুষ নন। গ্রিসের উপনিবেশ থেকে নানা দেশ ঘুরে, শেষতক এসে থিতু হন এথেন্সে। তাঁরা তৎকালীন নগর রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা দেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে মানুষকে ভাবিয়ে তোলেন। সোফিস্টরা সে-সময়ের উন্নত সভ্যতাগুলো, যেমন, পারস্য, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করে এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত, যেমন, লিবিয়া, সিরিয়া, থ্রাসিয়া দেশের সংস্কৃতির সাথেও তাদের পরিচয় ঘটে। এসব দেখে একটা স্বভাবতুল্যমন নিয়ে তারা এথেন্সে প্রবেশ করে। আমরা দেখি যে, সোফিস্টদের সেই ন্যায়-অন্যায়, রাষ্ট্র, মানুষ নিয়ে কেবল তোলা প্রশ্নগুলো সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মধ্যে দিয়ে এক চরম পরিণতি পায়, যা নির্মাণ করে সমস্ত ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তিমূল। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুগই হচ্ছে গ্রিক দর্শনের সবচেয়ে চরম উৎকর্ষের যুগ। থেলিস থেকে সেই পুরাণের বাইরে এসে মানুষের স্বাধীন জিজ্ঞাসার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা ক্রমশ পরিণত হয়ে এক পূর্ণবয়স্ক প্রাজ্ঞের রূপ নিল, এবং এসব ভাবনার কোনোটাই হঠাৎ-পেয়ে-বসা ভাবনা নয়। হোমারীয় যুগের শেষাশেষি যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমস্ত গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলোকে এবং তার উপনিবেশগুলোকে ভূতগ্রস্ত করে রাখে, তার অনিবার্য ফলস্বরূপ, সক্রেটিস রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তাঁর জিজ্ঞাসা দ্বারা সবাইকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। সক্রেটিসের করুণ মৃত্যুদণ্ড তাঁর শিষ্য প্লেটোকে দারুণভাবে ভাবিয়ে দেয়। সেই সাথে গ্রিসের দাস-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা নাগরিকদের প্রাচুর্য ও অবসর দিয়েছিল ঢের। যে প্রাচুর্য ও অবসর উত্তর-হেলোনিক যুগকে ধ্রুপদী যুগে রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এসব পরম্পরা আমাদের অজানা নয়, সেখানে প্লেটোর ‘আইডিয়া’ এবং সেই ‘আইডিয়া’ অ্যারিস্টটল কর্তৃক নাকচ করে দেয়া – এর মধ্য দিয়েই ইউরোপীয় দর্শনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমণ শুরু হয়।
এরপর হেলেনিক যুগে মানুষের সামনে সবচেয়ে প্রধান যে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, সে হচ্ছে, জীবনের পরম কল্যাণ কী? কারণ খ্রি.পূ. ৩২০ থেকে, ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান কর্তৃক প্লেটোর লাইসিয়াম বন্ধ করে দেবার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে উলেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। আলেকজান্ডারের বিশ্বজয়, তারপর গ্রিসের পতন, রোমের উত্থান, নাজারাথের যিশুর মঙ্গল-প্রচার – সব মিলিয়ে সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য যে-ব্যাপারটা ঘটে, সে হচ্ছে, রাষ্ট্রিক এবং সাংস্কৃতিক সীমারেখার অবলুপ্তি। স্বাভাবিকভাবেই স্বাজাত্যবোধ দ্বারা, স্ব-সাংস্কৃতিক তাড়না দ্বারা যে মানুষ আপন মনে আপন ঘরে মগ্ন হয়ে থাকতে পারত, হঠাৎ করেই নানা স্রোত এসে সেটাকে ঘুলিয়ে তুলল, এই ঢেউ মানুষের মনে সঙ্গত প্রশ্ন তুলল, সত্যিকারের সুখ কীভাবে অর্জন করা যায়? জীবনের পরম কল্যাণই-বা কীসে? এই আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার গর্ভ থেকে জন্মলাভ করে অ্যান্টিস্থেনিসের সিনিক দর্শন, জেনোর স্টোয়িক দর্শন, এপিকিউরাসের এপিকিউরীয় দর্শন এবং প্লটিনাসের নিও-প্লাটোনিজম। এ-সকল দর্শনের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসা ছিল, সত্যিকারের সুখ কীভাবে অর্জন করা যায়? এই যুগটাতে প্লটিনাসের আগ পর্যন্ত নতুন আর কোনো ভাবনার সাথে আমাদের যোগ ঘটে না।
তারপর সময়ের কাঁটা যখন রোম সাম্রাজ্যের বাইরে এসে দাঁড়াল, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীতে গথ, হুন, ভ্যান্ডাল প্রভৃতি উপজাতি কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ এবং রোমের পতনের পর ধীরে ধীরে প্রাচীন রোমান ঐতিহ্যের অবশেষকে অবলম্বন করে নবম ও দশম শতকে যে-সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান আদর্শিক এবং রাজনৈতিক অবলম্বন ছিল চার্চ। সে-এক অদ্ভুত অন্ধকার সময়। যা-কিছু মানুষের সহজাত, যা-কিছু সহজ – তার সবকিছুর উপরই চার্চের ভূত ভর করেছিল। যাবতীয় ঐহিক-ইন্দ্রিয়েচ্ছা সেখানে তুচ্ছ। গোটা মানবজীবনের সার্থকতা ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্তিতেই নিহিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, জীবনাচার – সবই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। এই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সামান্য যা উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হতো, তা সামন্তপ্রভু কর্তৃক আত্মসাতের জন্য সামরিক শক্তির সঙ্গে ধর্মীয় আদর্শেরও মিশ্রণ ঘটাতে হয়েছিল।
যা হোক, একাদশ ও দ্বাদশ শতকে উপজাতিদের আক্রমণক্ষুব্ধ তরল-তরঙ্গায়িত ইউরোপের সামাজিক প্রেক্ষণ জমাট বাঁধতে শুরু করে। নানাবিধ কারণে উৎপাদন শক্তির ক্রমোন্নতি ঘটে, উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে। ভূমধ্যসাগরের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের দূর-বাণিজ্য স্থাপিত হয়। সবকিছু মিলিয়ে ইতালির বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে নতুন যে বণিক ও কারিগর শ্রেণী গড়ে ওঠে, তারা গোটা উৎপাদন ব্যবস্থায় দারুণ এক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। এই সামাজিক প্রেক্ষণ থেকেই ত্রয়োদশ হতে ষোড়শ শতকের ইতালীয় রেনেসাঁসের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। ক্লাসিকাল যুগের শেষে এবং সামন্ততন্ত্রের বিকাশকালে গোটা ইউরোপে মানবসভ্যতাকে তার সর্বক্ষেত্রীয় সহজ-সুন্দরকে যে নিদারুণ বেদনায় কড়িকাঠে শুইয়ে দিতে হয়েছে – তাতে হতশ্রী সাধারণ মানুষ তাদের বিশুষ্ক জীবন, নিরুপায় মোহে সঁপে দিয়েছে চার্চের সেই আলো-আঁধারির সেই হাজার বছরের মৃত অন্ধকারে। সামন্তপ্রভু এবং চার্চের যাজকদের জীবন ছাড়া বাকি সবার জীবন এক নিদারুণ নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছিল। সে জীবনে জৈবিক আশ্বাস খুঁজতে চার্চের অন্ধকারে মুখ গুঁজে ধর্মস্তন পান করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না তাদের হাতে। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শতকে কৃষি ও শিল্পের ক্রমোন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নগরে বন্দরের বিকাশ, সাধারণ মানুষের জীবনে বেশ কিছুটা বৈষয়িক সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এক অদ্ভুত জীবনাবেগ সঞ্চারিত হয় গোটা ইউরোপে। কিন্তু সে নৈবেদ্য সাজাবার মতো থালা তখন সমকালীন সমাজে ছিল না। বিহ্বল মানুষ বিশ্বাস থেকে মুখ তুলে ধ্রুপদী গ্রিক শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনে আবার সর্বযোগ ঘটাল। তবে সে অর্থে রেনেসাঁস পুনরাবৃত্তি নয়, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকে উৎপাদন পদ্ধতিতে নতুন হাওয়া লাগায়, মানুষের জীবনে শ্রী ফিরে আসতে শুরু করে। তখন তারা জীবনের ইন্দ্রিয়কে কোনো আরোপিত শাসনে বদ্ধ না-করে, প্রাচীন ধ্রুপদী শিল্প ও সাহিত্যের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নতুন করে সাজিয়ে তুলল। এ-কথা আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি যে, প্রাচীন গ্রিসে কায়িক শ্রমের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সেখানে ফিডিয়াসের মতো ভাস্করকেও ব্রাত্যজন হিসেবে নিগৃহীত হতে হয়েছে। কিন্তু রেনেসাঁস যুগে এইসব সকরুণ বাদ-বিসম্বাদ যেন নিমেষেই চুকে গেল, সব অর্গল খুলে জীবনের মধ্যে বসে জীবনের শিল্পরসে মেতে উঠলেন শিল্পীরা, কোনো বাঁধ ভাঙতেই যেন বাধা নেই। সৃষ্টি হলো রাফায়েলের লেডা, মাইকেলেঞ্জেলোর অ্যাপোলো, লিওনার্দোর মোনালিসা, বতিচেলির ভেনাস, পেত্রার্কার লরা, দান্তের বিয়াত্রিচে – সে এক অনুপম সৃষ্টি মহিমা, অমিত রস-লাবণ্য।
এভাবে মানুষকে কেন্দ্রে এনে যে মানবিক জিজ্ঞাসা, যে মানবিক বিনিময় – মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে সভ্যতার, শুরু হলো – তা অনেক আঁকাবাঁকা গলি ঘুরে রিফর্মেশনের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকে ফরাসি আলোকপ্রাপ্তি আান্দোলনের জন্ম দেয়। এর মাঝখানে শুরু হয় জ্ঞানতত্ত¡ নিয়ে মানুষের বচসা – প্রজ্ঞা না ইন্দ্রিয়, কার মাধ্যমে সত্যিকার জ্ঞান-বিকাশ লাভ ঘটে; বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদীদের সুদীর্ঘ নান্দনিক যুদ্ধ কান্টে এসে থিতু হয়। প্লেটোর মতো একেবারেই আনকোরা ভাবনায় মানুষকে ভাবিয়ে তুললেন দেকার্তে। সেখান থেকেই আবার এক নবযাত্রা। এভাবেই একসময় যুক্তিক্লান্ত মানুষ আশ্রয় খুঁজলেন কল্পনায়, অনুভূতিতে, স্বপ্নে – যা কিছু ধরা যায় না, পাওয়া যায় না, সে-সকল সুন্দরে। তুমুল আকার ধারণ করল রোমান্টিক আন্দোলন। যেমন হয় আর-কী, শাঁস শুকিয়ে গেলে ছোবড়া পড়ে থাকে, ঠিক তেমনি রোমান্টিক আন্দোলনের সারবত্তার যখন তুঙ্গ থেকে অবরোহণ শুরু হয়েছে, হেগেল এসে উদ্ধার করলেন তাকে। রোমান্টিকরা সবকিছু ভুতুড়ে সেই বিশ্বচিদাত্মায় লীন করে চুপচাপ স্বপ্ন দেখছিলেন। হেগেল তাকে মাটিতে নামিয়ে এনে মানবিক রূপ দান করলেন। অবশেষে একদিকে কার্ল মার্কস গভীরভাবে ইতিহাসকে বুঝে নিয়ে তার পরিবর্তনের ধারাকে আত্মস্থ করে বসলেন – এতদিন দার্শনিকেরা ইতিহাসকে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন, এবার প্রয়োজন ইতিহাসকে পাল্টানো। অন্যদিকে, অস্তিত্ববাদীরা এসব কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ব্যক্তিই হচ্ছে আসল – একমাত্র গণ্য। এই হচ্ছে অতি সংক্ষিপ্ত পরম্পরা। এই সুদীর্ঘ অতিক্রমণে কোনো ভাবনাই কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়। সকল ভাবনাই তার সময়ের সার্বিক বাস্তবতার সাথে, গভীর সখ্যে গাঁটছড়া বেঁধে আছে – সেই ইতিহাসটা না বুঝলে বিচ্ছিন্ন দর্শন জ্ঞান ব্যর্থ।
বিচ্ছিন্নভাবে ভাবনাগুলোর বর্ণনা বড়ো বেশি কানে বাজে, তাকে ঘনিয়ে, ফেনিয়ে, তখনকার সবগুলো ঢেউয়ে ডুবিয়ে তরঙ্গায়িত করে তুললে, তবেই না তা কান থেকে প্রাণের পরে গিয়ে পৌঁছে। শুধু পৌঁছে কেন বলছি, সেই পরিবেশনটাই সে-ভাবনা সম্পর্কে সত্য লাভ ঘটিয়ে দেয়। দীর্ঘকাল ধরে আমরা বার্ট্রান্ড রাসেলের History of Western Philosophy দ্বারা যে-কারণে তৃপ্ত ছিলাম, তা হচ্ছে এই, History of Western Philosophy সত্যিকার অর্থেই ঐরংঃড়ৎু. মানুষের ভাবনা যে কত অনিবার্যভাবে, কত বিচিত্রভাবে সময়ের নিগড়ে বাঁধা, আমরা রাসেলের বইখানিতে তাই দেখি। আর সোফির জগৎ অনন্য সোফি’র জগতের কারণে। যে জগৎ ১৫-তে পা দিতে যাওয়া একজন মেয়ের গভীরে গার্ডার নিপুণ হাতে সূচীকর্ম-দক্ষতায় বুনে তুলেছেন। ১৫-তে পা দিতে যাওয়া একজন মেয়ে সোফি, যার জগতে কৈশোরক আবেগ, খুনসুটি, ঘোর-লাগা স্বপ্ন আর অভিমান ছাড়া আর কিছু সাধারণভাবে থাকার কথা নয়। ইয়স্তেন গার্ডার সেখানে অসামান্য সব মণিমুক্তা দিয়ে সযতেœ সাজিয়ে তুলেছেন।
৩.
সোফি অ্যামুন্ডসেন ও আমাদের উত্তরাধিকার
সোফি অ্যামুন্ডসেন, জোয়ানা যার বান্ধবী, সামনে ১৫ই জুন, যে ১৫-তে পা দেবে। হঠাৎই এক আশ্চর্য চিঠি পায় তার ডাকবাক্সে। তাতে লেখা – কে তুমি? পৃথিবীটা কোথা থেকে এল? / সোফি কে? – সোফি, সোফি অ্যামুন্ডসেন – সহজ উত্তর। কিন্তু একটু ভাবতে যেয়েই দেখল যে এই উত্তরটা তাকে তৃপ্ত করছে না। সে লক্ষ করল যে গোড়াতেই একটা চরম অযৌক্তিক ব্যাপার তার উপর চাপানো হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, সে দেখতে কেমন হবে সে-ব্যাপারে তার কোনো মতামত নেয়া হয়নি। তার চেহারা স্রেফ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সে তার বন্ধু-বান্ধবদের বেছে নেবার অধিকার পেয়েছে, কিন্তু সে নিজেকে বেছে নেবার অধিকার পায়নি। শুরু হলো অ্যালবার্টো নক্সের কাছ থেকে আসা একের পর এক বিস্ময়কর সব চিঠি। তাতে সব নতুন নতুন জিজ্ঞাসা, যে-সব জিজ্ঞাসার সাথে এর আগে কখনো তার পরিচয় ঘটেনি। বইটি পড়তে যেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে ফেলতে হয়, যে এটা সত্যিকার অর্থেই দর্শনবিষয়ক একটা উপন্যাস। স্বাভাবিকভাবে একটা উপন্যাসে তার শিল্পবুননের মাধ্যমে যে আয়নাটা মেলে ধরা হয়, এবং সে আয়নায়, উপন্যাসে কথিত মানুষগুলোর মানসিক, ব্যক্তিক এবং সর্বোপরি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খুঁটিনাটি যেভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তা এখানে অনুপস্থিত। সে অনুপস্থিতি সঙ্গত কিনা, পাঠকের দিক থেকে তা বুঝে উঠা দুষ্কর। যেমন ধরা যাক, সোফি অ্যামুন্ডসেন, পঞ্চদশী বালিকা, জোয়ানা যার বান্ধবী; এ হচ্ছে সেই বয়স, যে বয়সে স্বপ্ন, চাঞ্চল্য, ঔৎসুক্য – সব মিলিয়ে একটা স্বপ্নাতুর ঘোরে কাটে মানুষের। এ হচ্ছে স্কুল থেকে বান্ধবী জোয়ানার সাথে ফেরবার পথে রোবট নিয়ে কথা বলবার বয়স, আর যা সহজে মানিয়েও যায়। কিন্তু যখন হঠাৎ করে কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি, যাতে লেখা, কে তুমি? তা সোফি নামের এই পঞ্চদশী বালিকাকে তখন চিরকালের এই দার্শনিক প্রশ্নটা সহজেই জিজ্ঞাসু করে তুলবে – এটা অনভিপ্রেত। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই আমরা দেখি, একের পর এক আসতে থাকা বিস্ময়কর প্রশ্নগুলো একেকজন দার্শনিকের মূল দর্শনচিন্তাকে পরিবেশনের আগে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দ্বারা সোফিকে ভাবিয়ে তোলার চেষ্টা, তখন আমরা বুঁদ হয়ে যাই এই দার্শনিক প্রকল্পের মধ্যে। উপন্যাসের শিল্পরস তখন এহবাহ্য। আর এটাকে উপন্যাসই ভাবতে হবে, তা কতটুকুই-বা সঙ্গত হতে পারে। এটা হচ্ছে তাই – যা লেখা হয়েছে। কারণ এত গভীর দর্শনগুলোকে রসোত্তীর্ণ করে, নানা অভিনব প্রক্রিয়ায় যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে আর সব না-প্রাপ্তি তুচ্ছ হয়ে যায়।
পুরো সোফির জগৎটাকে যোগ্যভাবে দাঁড় করাবার জন্য ইয়েস্তেন যে-দুটো কুশলীপনার সাহায্য নিয়েছেন, তার একটা, যার দায় পুরো দর্শন কোর্সটাকে ১৫ বছরে পা রাখতে যাওয়া একজন মেয়ের বুদ্ধিগাম্য করে তোলার কাছে; সে দায় হচ্ছে, কোন্ সময়ের দর্শনকে কীভাবে পরিবেশন করলে, তাকে যথার্থভাবে পরিবেশন করা যায়। অন্যদিকে হিল্ডারহস্য। হিল্ডারহস্যের মধ্য দিয়ে পুরো গল্পটাকে রহস্যগল্পের ঢঙে, আদ্যোপান্ত সরস আমেজে, বিয়ার্কলের দর্শনকে ব্যবহারিক করে তুলেছেন।
সমগ্র প্রাচীন যুগটাকে, দর্শনের জন্ম থেকে শুরু করে সেমেটিক জাতি ও গ্রেকো-রোমান সভ্যতার মিথস্ক্রিয়া পর্যন্ত, অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিঠির মধ্য দিয়ে অভিনব প্রক্রিয়ায় সোফির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাচীন যুগের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রত্যেক দার্শনিকের ভাবনার মূলসূত্রটি ধরিয়ে দেবার জন্য, সরাসরি তাঁর দর্শনের উপর একটা জ্ঞানগর্ভ চিঠি না-লিখে, প্রথম চিঠিতে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন তুলে, সোফির মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাকে উসকে দেয়া হয়, যে জিজ্ঞাসা দিয়ে আলোচ্য দার্শনিকের দর্শন অনুসন্ধিৎসার জন্ম হয়েছিল।
শুরু হয় দর্শনের জন্মকথা দিয়ে, ‘দু’হাজার বছর আগের এক গ্রিক দার্শনিক বিশ্বাস করতেন দর্শনের জন্ম মানুষের বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতার মধ্যে। বেঁচে থাকাটা এত আশ্চর্য বলে বোধ হয়েছিল মানুষের কাছে যে আপনা থেকেই দার্শনিক প্রশ্নগুলো জেগে উঠেছিল তাদের মনে।’ তারপর পৌরাণিক বিশ্বচিত্রে পুরাণ কীভাবে মানুষের ভাবনা-জগৎকে দখল করে রেখেছিল, কীভাবে খ্রি.পূ. ৬০০ সালের আগে মানুষের সকল জিজ্ঞাসা ঘুমে বিবশ ছিল এবং থেলিস থেকে কীভাবে সে-সকল ঘুমিয়ে থাকা জিজ্ঞাসার পুনর্জাগরণ ঘটল – এসব বর্ণনা যথার্থ সামাজিক আবহের ওপাশ থেকে না বর্ণিত হলেও বর্ণনার আন্তরিক ঢঙটির কারণে সেটাকে কখনই নিরাভরণ মনে হয়নি। এভাবেই প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের প্রকৃতির মৌলগঠন বিষয়ক ভাবনা, সোফিস্টদের মানবকেন্দ্রিক ভাবনা, সক্রেটিস প্লেটো-অ্যারিস্টটল হয়ে হেলেনিক যুগ এবং অতঃপর সবচেয়ে অসাধারণভাবে বর্ণিত গ্রেকো-রোমান ও সেমেটিক সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া; এ-পর্যন্ত চিঠির মাধ্যমেই সোফিকে ভাবিয়ে তোলা ও প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হচ্ছিল। কিন্তু মধ্যযুগ পর্বে, নিছক একেঘেয়েমি কাটানোর দায়ই শুধু নয়, অত্যন্ত অভিনব এবং রসোত্তীর্ণ প্রক্রিয়ায় যা ১৫ বছরের মেয়ের জন্য সহজগম্য; গার্ডার অ্যালবার্টো এবং সোফিকে মুখোমুখি করবার মাধ্যমে মধ্যযুগকে হাজির করলেন – সেন্ট মেরি গির্জায়। সমগ্র সোফির জগতের মধ্যে দর্শন বা মানুষের মহোত্তম ভাবনাগুলো কীভাবে গোটা সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার গর্ভ থেকে জাত, তার সবচেয়ে সফল বর্ণনা পাই গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতি এবং সেমেটিক সংস্কৃতির মিলন থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত; ১৫ বছরের বালিকার কাছে, ভোর আটটায়, সেই প্রাচীন সেন্ট মেরি গির্জাতে পুরো মধ্যযুগটা অভিনব প্রক্রিয়ায় রাত বারোটাকে ০ ঘন্টা করে এক হাজার বছরের হিসাব উলেখযোগ্য সন তারিখসহ যেভাবে উপস্থাপন করলেন, তাতে যারপরনাই আমরা অভিভূত হই। কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসেবে বারবার গোপনে একটা প্রশ্ন পিষে মারে, সে হল, কেন মানুষেরা গ্রিক এবং হেলেনিক সংস্কৃতির সেই মহান যুক্তিবাদের পথকে পরিহার করে এমন বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। একথা বারবার বলেই প্রধান করে তুলতে হবে যে আর্থ-সামাজিক বা¯তবতার যথার্থ বর্ণনা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ভাবনাই ঐক্য তৈরি করতে পারে না। গোটা মধ্যযুগে রাজনীতি সংস্কৃতি আর অর্থনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অর্থনীতিতে তখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনে সীমাহীন দারিদ্র নেমে এসেছে। রাজনীতিতে পোপ-ই হলেন সর্বমান্য ব্যক্তি। কিন্তু কী সে-ই অন্তর্গত কারণ যা-কিনা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের সহজ স্বাভাবিক প্রকাশগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। সেই বর্ণনা থেকে অর্থাৎ সার্বিক প্রেক্ষণ থেকে সে দর্শন উঠে এসেছে, তার সফল বর্ণনা পাই এই মধ্যযুগ পর্যায়ে এসে। গোটা প্রাচীন যুগ ভেতরে ভেতরে বারবার আমাদের মুখিয়ে তোলে, কী সেই কারণ যার জন্য খ্রি.পূ. ৬০০ সালে এসে মিলেশিয়ান স্কুলের দার্শনিকেরা হঠাৎ করে এক জিজ্ঞাসার পথে মানবসভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন? কী সেই অন্তর্গত তাপ, যাতে কিনা গোটা গ্রিসকে যুক্তি ও ভাবনার ভূতে পেয়ে বসেছিল? এসব কারণ খুব দূরগম্য, তা নয়। কী কারণে দীর্ঘকাল আমরা প্লেটোর রিপাবলিককে ‘মিথ অব স্পার্টা’ (সুঃয ড়ভ ংঢ়ধৎঃধ) বলে এসেছি, তা স্পষ্ট না-হলেও অনুমেয়।
সেন্ট অগাস্টিন এবং টমাস অ্যাকুনাইসে দার্শনিক ঔদার্য মধ্যযুগীয় অন্ধকারে জোনাকির আলো-তুল্য আশ্বাসের মতো দেখালেও, এক হাজার বছর চার্চের সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মানবসভ্যতার যে সীমাহীন অপমান ঘটছে, তার কাছে সেই আলোর ঔজ্জ্বল্য আর যাই হোক কোনোভাবেই আমাদের আশ্বস্ত করবার মতো নয়। জমকালো রাজা-মহারাজা আর বীরধর্মব্রতী নাইটদের গল্প যতই আমাদের রাতগুলোকে ঘুমহারা করে রাখুক না কেন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন যে নিদারুণ দারিদ্রে শ্রীহীন বিশুষ্ক ফলের মতো অসহায় অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল, চার্চের নিষ্ঠুর শাস্ত্রাচারের জন্য হাজার বছর ধরে যে-মূল্য মানুষকে দিতে হয়েছে, তা কোনো ভাব বা ভাবনাই আমাদেরকে বিস্মৃত করতে পারে না। তার উপর যে-কোনো আদর্শায়ন আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। একথা সত্যি যে, কোনো যুগই পুরোপুরি ভালো বা পুরোপুরি খারাপ নয়। প্রতি যুগের মাঝেই ভালো মন্দের দুটো সুতো জড়াজড়ি করে থাকে। তবে যে-কোনো সমগ্রের মধ্যে বর্তমান তার প্রতি ক্ষুদ্র অংশ যেমন বিচ্ছিন্ন একটা অর্থ বহন করে, যে অর্থ কোনোভাবেই সমগ্রকে প্রকাশ করে না; তেমনি, সমস্ত ক্ষুদ্রাংশ মিলে তার যে সমগ্রতা, তা আমাদেরকে একধরনের সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত দেয়। গোটা মধ্যযুগে বিচ্ছিন্নভাবে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, তার সম্পূর্ণ চেহারাটা আমাদের কাছে এই। তাকে আইডিয়ালাইজ করার চেষ্টা এবং একই সাথে খ্রিস্টতত্ত্বের উপর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত আমাদেরকে দারুণভাবে ব্যথিত করে। বালিকা সোফির জগৎ যে কত সহজেই আমাদের জগতে ঢুকে পড়ে, তা নিবিষ্ট আমরা সহজেই টের পাই। এতই চমকে দেবার মতো উপস্থাপনা তার, এতই বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতা তার, সেখানে নৈর্ব্যক্তিকতার সামান্য বিচ্যুতি আমাদেরকে অভিমানী করে তোলে।
৪.
দেকার্তে থেকে আধুনিক দর্শনের শুরু। দর্শনের সাধারণ পাঠক হিসাবে আমরা গভীর বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করি, গার্ডার দেকার্তের দ্বৈতবাদ, স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধিবাদী ও অস্তিত্ববাদীদের প্রায় মল-যুদ্ধ-তুল্য-দ্বন্দ্ব কীভাবে ১৫ বছরের বালিকার বুদ্ধিগম্য এবং আবেগগম্য করে তোলেন। দেকার্তের প্রকল্পের শুরু হয় সন্দেহ দিয়ে। এ-সন্দেহ সমস্ত উত্তরাধিকারের প্রতি সন্দেহ। তিনি চাইছিলেন পায়ের নিচে শক্ত মাটি। এই সন্দেহের পথে যেতে যেতেই একসময় একটা ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ হন, আর তা হলো, তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। সেখান থেকেই সেই অতি বিখ্যাত কথাটির চল ঘটে, think, therefore I exist. এ-সব সাধারণ বর্ণনার মধ্য দিয়েই সোফির কাছে উপস্থাপন করা হয়। দেকার্তের নিখুঁত সত্তার অস্তিত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তটা বেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে অ্যালবার্টোর বর্ণনা এবং সোফির অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই, দেকার্তের মতো অতিসাবধানী লোকের কাছ থেকে নিখুঁত সত্তা সম্পর্কিত এসব আত্মবিশ্বাসী বর্ণনা শোনবার সময়, সহজ সে-সব প্রশ্নগুলো সহজেই মনে উঁকি দেয়। গার্ডার সে-গুলোকে এড়িয়ে না-গিয়ে, বা বর্ণনার ঢঙে সে-গুলো উপস্থাপন না-করে, সোফির মুখ দিয়ে তা বলিয়ে নিলেন। ক্রকোফ্যান্টের ধারণা থাকার মানেই তো এই নয় যে ক্রকোফ্যান্টের অস্তিত্ব আছে। এ-ধরনের পারস্পরিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সোফির সাথে সাথে আমরাও বুদ্ধিবাদী দেকার্তের দার্শনিক প্রকল্পের মধ্যে ঢুকে সহজেই বের করে আনি যে তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি, নিখুঁত সত্তা বলে কোনো কিছু অস্তিত্বমান এবং বাহ্যিক বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে । এবং সেখানে থেকে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে দেকার্তের দ্বৈতবাদ বুঝে উঠে সোফির সাথে সাথে যারপরনাই বিস্মিত হই। কিন্তু পুরো ‘সোফির জগৎ’-এ সোফির উপর যে-ধরনের ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাতে করে ‘মন আর দেহের মধ্যে সংযোগ পিনিয়াল গ্ল্যান্ড দ্বারা’ – এ-ধরনের স্রেফ কল্পনাপ্রসূত অ-দর্শন বুদ্ধিবাদী দেকার্তের, যিনি কিনা দর্শনের ঘরে অতীতের সব জঞ্জাল সরিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিতে চেয়েছিলেন, কাছ থেকে জানবার পরে তা সোফির চোখে মুখে প্রকাশে কোনো জিজ্ঞাসার জন্ম না-হওয়া একধরনের বিস্ময় তৈরি করে বৈকি। সোফি অ্যামুন্ডসেন বিস্মিত হতে জানে, নিজের প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করতে জানে। এই সময়ের একজন মানুষ হিসেবে, তার বিস্ময় নতুন কোনো ভাবনার সাথে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপার হয়ে উঠবে – এটা অভিপ্রেত। কিন্তু, বারবার এটা অত্যন্ত দুঃখের সাথে যেন মেনে নিতে হয় যে, দার্শনিক কল্পনায় দর্শন যেখানে জঞ্জাল হয়ে উঠেছে, যা হয়ত ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে সম্পদ ছিল, তা সোফির মধ্যে এই সময়ের সোফি হবার পরেও কোনো জিজ্ঞাসার জন্ম দেয় না।
তবে অদ্বৈতবাদী স্পিনোজাতে সোফির জিজ্ঞাসাকে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ ও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। বারুচ স্পিনোজা দেকার্তের দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে বসলেন। অস্তিত্বশীল যে কোনো বস্তু হয় চিন্তা নয় ব্যাপ্তি, দেকার্তের এই ভাবনা স্পিনোজা কমিয়ে এনে স্রেফ সারবস্তু (substance) হিসাবে ঘোষণা করলেন – এ পর্যন্ত আমাদের কাছে সহজমান্য। কিন্তু, এই সারবস্তুকে যখন তিনি ঈশ্বরের মাঝে লীন করে দিলেন এবং অ্যালবার্টোর মুখে এসব কথা যখন সোফি শুনে যাচ্ছে, তখন দর্শনের জমিতে সেটা যতই মানানসই হোক না কেন, সোফির চোখে দেকার্তের ঐ অংশের মতো আরোপিত কোনো বিস্ময় জমিয়ে তুললে সে বড়ো বেমানান হতো। কিন্তু এখানে এসে আরেকবার সিদ্ধহস্ত গার্ডারের দেখা পাই। সোফির মুখ দিয়ে তিনি বলিয়ে নিলেন, ‘… আমি যখন চলাফেরা করি, তখন এই চলাফেরাটা করছি আমিই, তার মধ্যে ঈশ্বরকে জড়াতে হচ্ছে কেন?’ সোফির এই অকপট সরল জিজ্ঞাসায় স্পিনোজা অংশের আলোচনাটা আরো সরস হয়ে উঠেছে। প্রতিটা বস্তু যে কত অনিবার্যভাবে তার অভ্যন্তরীণ কারণের জন্য সে যা করে – তার বাইরে আর কিছু করতে পারে না, তা আমরা দেখতে পাই। অনামিকা তার অনামিকাত্বের কারণেই হাতের বুড়ো আঙুলের মতো গুনতে অক্ষম, এসব ভাবনা আমাদেরকে একই সাথে ব্যথিত এবং অভিভূত করে ।
যা হোক, কন্টিনেন্টাল বুদ্ধিবাদ শেষতক গড়িয়ে গড়িয়ে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদের গায়ে গিয়ে অনিবার্য সংঘাত বাঁধিয়ে বসবে – এটা পূর্বঅভিপ্রেত। আমরা অপেক্ষা করে থাকি, বুদ্ধিবাদী আর অভিজ্ঞতাবাদীদের এহেন মলযুদ্ধ কী প্রক্রিয়ায় সোফির কৈশোরক বিস্ময়ের দ্বারে অভিঘাত তোলে। নতুন নতুন শব্দের তোড়ে বাতাসটা সবে যখন ভারী হতে শুরু করেছে তখন সোফির প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা আমাদের আশ্বস্ত করে, কীসব কঠিন কঠিন শব্দ, অভিজ্ঞতাবাদটা কী আবার একটু বুঝিয়ে বলুন। এভাবে দর্শনকে কখনও হাওয়ায় ভাসিয়ে, কখনও মাটিতে নামিয়ে এনে, গার্ডার দর্শনকে জীবনের অন্তরঙ্গ রসে ডুবিয়ে স্বাদু করে তুললেন।
তবে হিউম অংশে ‘অহং’ আলোচনা প্রশ্নে যখন বুদ্ধের কথা তোলা হয়, তখন এসব ছাপিয়ে ভেতরটা একধরনের চাপা-বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে। কারণ, বহুবিচিত্র গোটা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস থেকে, মাঝখানে, হঠাৎ একজনকে পেড়ে এনে বিচ্ছিন্নভাবে পূর্বাপর সংযোগ ছাড়া উপস্থাপন করায় ভারতীয় সাংখ্য দর্শন, নৈয়ায়িক দর্শন, চার্বাক দর্শন, জৈন দর্শন … এ-সকল অসাধারণ ‘স্কুল অব থট’ (School of thought) একধরনের সচেতন উপেক্ষায় অপমানিত হয়ে ওঠে। বুদ্ধ প্রসঙ্গ না-এলে হয়ত মেনে নিতাম যে, না এটা পাশ্চাত্যের দর্শনবিষয়ক একটা উপন্যাস। কিন্তু সোফির কৈশোরক বিস্ময় আর আবেগ চোখে পুরে আলবার্টো নক্সের সাথে আমরা যতই এগোতে থাকি, ততই সত্যিকারের দর্শন ও জীবন-অভিজ্ঞতা লাভের পাশাপাশি খ্রিস্টতত্ত্বের প্রতি একধরনের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত, ভারতীয় দর্শনের প্রতি সচেতন উপেক্ষা, আমাদেরকে আবার ভয় পাইয়ে দেয়, যে ভয় হালে আরো মানুষের আরো জল পেয়ে স্ফীত হয়ে উঠেছে – সারা পৃথিবীতে সভ্যতার ইতিহাস মানেই ইউরোপ। অথচ আমরা ইতোমধ্যেই বুঝে গেছি যে, হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষমতা, পুঁজি, মানবসভ্যতার উপর সিন্দবাদের ভূতের মতো এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, ইউরোপ ছাড়া সারা পৃথিবীর অন্যসব কম-আলো-সভ্যতার বেদনা-জীর্ণ জীবন-মথিত যে-সকল সুকুমার অর্জন, মানবিক উৎকর্ষ – তা পুঁজির দাপটে, ক্ষমতার বিশ্বায়নে, ঔপনিবেশিকতার কানাগলিতে পড়ে মূলস্রোত থেকে ছিটকে পড়েছে। আমরা এখন সেই নিদারুণ বেদনার, কঠিন অপমানের অবসানের যুগে এসে গেছি। তাই এরকম অসামান্য কীর্তি বারবার অভিভূত করবার পাশাপাশি, কী এক সূক্ষ্ম অভিঘাতে গভীরে গোপন বেদনা জাগিয়ে তোলে।
৫.
রোদ খুব চিন্তা করে চিলতে হয়ে আসে
এভাবে মানবসভ্যতার ভাবনা-ইতিহাসের পরম্পরার সাথে একের পর এক যোগ ঘটে সোফির। সোফি, সোফি অ্যামুন্ডসন, জোয়ানা যার বান্ধবী, স্কুলের চৌহদ্দি, মাঝে মাঝে জোয়ানার সাথে ক্যাম্পিং-এ যাওয়া, সাধারণ কৈশোরক গণ্ডি ছাড়া সাধারণভাবে আর কোনো কিছুতেই যার মন যাবার কথা নয়; সে মন এক দারুণ ঊৎকণ্ঠায় ভরে থাকে এখন। তারপর? তারপর কী হলো? বুদ্ধিবাদী আর অভিজ্ঞতাবাদীদের চাপাচাপিতে দর্শন যে এক কানাগলিতে এসে ঠেকল, কে তাকে উদ্ধার করল? আর শেষতক সত্যই-বা কোনটা? … সত্য কে জানে? তবে কোনো ভাবনাই যে বিচ্ছিন্ন নয়, সব ভাবনাই যে বহন করে তার পূর্বতনের যোগ্য উত্তরাধিকার। এবং এসব ভাবনা যে নিছক ভাবনা নয়, তার সাথে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বেঁচে থাকা জড়িত না-থাকলেও, আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সাথে সেসব ভাবনা যে দুর্বোধ্য গাঁটছড়া বেঁধে আছে – সেই প্রত্যয় জন্মে সোফির মাঝে। তার অবসর এখন মায়ের বকুনি খাওয়ার পরে নিছক বিষণ্ন বিকেল কাটাবার মতো বিবর্ণ নয় – সে অবসর এখন রোমান্টিকদের ডানায় ভর করে সারা ইউরোপ উড়ে বেড়াতে জানে। সোফির স্কুলের ধর্ম পরীক্ষা এখন নিছক পরীক্ষা নয়, সে পরীক্ষা ভাবনায়, মননে, বেদনায়, অভিজ্ঞতায় একধরনের নিজের সাথে নিজের নিবিড় বোঝাপড়া। সোফি বুঝে ফেলে মানুষের মূর্খামি। কত শত বছর ধরে নিবিষ্ট ভাবনা ভেবেও মানুষ স্থির করতে পারেনি যে, জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আসলে ইন্দ্রিয় না প্রজ্ঞার মাধ্যমে ঘটে। অথচ মানুষ কী নিশ্চিতভাবেই না এসব ব্যাপারে প্রশ্নহীন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে।
জগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জন হয় ইন্দ্রিয় না হয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে, এ দুইয়ের দ্ব›দ্ব দর্শনকে যে বদ্ধপথের শেষ মাথায় নিয়ে গিয়েছিল, কান্ট তা থেকে তাকে উদ্ধার করেন। তবে এ কথা মানতেই হয়, কান্টের Categorical imperative ব্যাখ্যার সময় ‘সোফির জগৎ’ যেন তার সহজ সরসতা হারিয়ে কিছুটা অকারণ সরব হয়ে উঠেছে। যদিও মনোযোগী সোফি তাতেও মুগ্ধ। এভাবে বার্কলে, বিয়ার্কলে, ফরাসি আলোকপ্রাপ্তি, রোমান্টিক আন্দোলন, আরও নানা ডানায় ভর করে দর্শন রোমান্টিসিজমের বৈধ উত্তরসূরি হেগেলের যুগে এসে পা রাখে। আমরা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসি। কারণ একথা তো বলা যায়ই যে, ইউরোপ তার মননের দেহে যৌবন পেয়েছে হেগেলের দর্শনের মধ্য দিয়েই। জার্মানি তখনো সামন্ততান্ত্রিক খোলস ছেড়ে বের হতে পারেনি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা তখনও দূর-স্বপ্ন, দূরে খুব ক্ষীণ শিখায় কেবল আশা জাগিয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। ষোড়শ শতকের সেই কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর থেকে রিফর্মেশন স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অধিকারের যে আশ্বাস দিয়েছিল, বাস্তবে তা ফুল হয়ে ফুটতে পারেনি, সব সম্ভাবনা মুকুলেই রয়ে গেছে। রাষ্ট্র তখনও চোখ পাকিয়ে জনগণের সকল স্বাধীনতার সকল গতি রুদ্ধ করে রেখেছে। তার মধ্য দিয়ে জার্মানি আদর্শবাদ চিন্তার নবদিগন্ত স্পর্শ করে স্বাধীন-চিন্তাকে পূর্ণতা দিয়েছে। হেগেল রোমান্টিকদের ভুতুড়ে বিশ্বচিদাত্মা ইতিহাসের মধ্যে লীন করে দিয়ে আমাদেরকে নতুন এক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন। যেখান থেকে শুরু হলো মানবসভ্যতার মানবিক ইতিহাসের নতুন এক অভিযাত্রা। কিন্তু ‘সোফির জগৎ’ থেকে আমরা কোনোভাবেই হেগেলের সেই বিশালত্বের কোনো খোঁজ পাই না। বিপুল বিস্তারিত এক নদী মোহনায় এসে হঠাৎ করেই যেন ক্ষীণাঙ্গী হয়ে গেল।
মার্কসের অংশ আমাদের শুধু হতাশই করে না, মার্কসের অসম্পূর্ণ এবং একপ্রকারের ভুল ব্যাখ্যা আমাদেরকে রীতিমতো কাতর করে তোলে। … সেই অদ্ভুত বনের মধ্যে সোফি যখন দরিদ্র দেশলাইওয়ালী মেয়েটার সাথে অতি ধনী ব্যবসায়ীটির মুখোমুখি করিয়ে দেয়, তখন সোফি বলে, ‘এই মেয়েটি যাতে আরো ভালো একটা জীবনযাপন করতে পারে সেটা কিন্তু আপনাকে দেখতেই হবে।’ লোকটা তার হিসেবের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ‘এ-সমস্ত ব্যাপারে টাকা লাগে, আর আমি তো বলেইছি যে একটা পয়সাও বাজে খরচ চলবে না।’ …গরীব মেয়েটি বলল, ‘আপনি যদি আমায় সাহায্য না করেন, তবে আমি মরে যাব।’ … এভাবে মেয়েটি একসময় বলল, ‘আপনি যদি আমায় সাহায্য না করেন, আমি বনে আগুন ধরিয়ে দেব।’ – এরকম একটা রূপক গল্প-ছবির মধ্য দিয়ে মার্কসের দর্শনকে হাজির করা হয়। দরিদ্র মেয়েটি কখনোই তাকে বলে না যে আমাদের হিসেবটা ঐতিহাসিক, কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়।
মার্কসীয় দর্শন যে কোনো স্বপ্ন-কল্পনা নয়, এটা অতি সাধারণভাবেও স্বীকৃত। সেখানে দরিদ্র মেয়েটার আকুতি এক ধরনের আদর্শবাদের পক্ষ থেকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য নিরসনের ইচ্ছার কথা মনে করিয়ে দেয়। তা ছাড়া পণ্য প্রসঙ্গে মার্কসের যে তত্ত¡, বস্তু কীভাবে মূল্য পায়, মূর্ত শ্রম, বিমূর্ত শ্রম, ব্যবহারিক মূল্য, বিনিময় মূল্য – সে-গুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট আর অসম্পূর্ণভাবে এসেছে। মধ্যযুগ যেমন সপ্রতিভভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত, মার্কস তেমনভাবে নন। অথচ গোটা মার্কসবাদ বোঝবার পক্ষে পণ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস ‘Capital’-এ শুরুই করেছিলেন পণ্য থেকে।
আরো যে প্রশ্নটা আমাদের ভাবিয়ে মারে, সে হচ্ছে, কিয়ের্কেগার্ডের উপর আলাদা একটা অধ্যায় হতে পারলে সার্ত্রের উপর কেন নয়? সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটা নৈর্ব্যক্তিকতার বাইরে এসে ব্যক্তিক সুর বেজে ওঠে। সে সুর কখনো করুণ, কখনো উদ্বেগ-জাগানিয়া। তবে শেষতক ডারউইন, ফ্রয়েড হয়ে মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে যেভাবে ‘সোফির জগৎ’ নির্মিত হয়, তাতে সব মিলিয়ে একটা ঐক্য – সে ঐক্য ভাবনার, একটা সংহতি – সে সংহতি মননের, একটা সুন্দর, সে সুন্দর ঐতিহ্যের, ইতিহাসের, সর্বোপরি – মানবিক পরম্পরার একটা অপার বিস্ময় – সে বিস্ময় জীবনের, আমাদেরকে বহুযতেœ একটু একটু করে জাগিয়ে তোলে। এখানেই বোধ করি ‘সোফির জগৎ’ অনবদ্য।
৬.
বাংলা সোফির জগৎ
কে যেন বলেছিল, বাঙালির আবেগ জীবনের অনুপম সন্ধিক্ষণে দানা বাঁধলেও মননের ক্ষেত্রে সেই আবেগ বেশিরভাগ সময়ই বিদীর্ণ। তাই তার আবেগ সংহত হয় সঙ্গীতে, কাব্যে। সেখানে সে ধীবর-ঔৎসুক্যে ছিপ ফেলে বসে থাকে। সেখানে সে আমৃত্যু যৌবনপিয়াসী। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে মননের ভাষায় কথা বলতে কোথায় যেন তার বাধা, যত গভীরই তার ভাবনা হোক না কেন, তার প্রকাশ ঘটে সঙ্গীতে, কাব্যে, একটা ‘রিপাবলিক’-এর মতো করে নয়। আমাদের ছেলেবেলার বেড়ে ওঠার ছকেও একটা আলাদা হিসাব থাকে কাব্যের জন্যে, একটা বাড়তি ভালোবাসা থাকে সঙ্গীতের জন্যে, সেটা স্বাস্থ্যপ্রদ – স্বীকার করি; কিন্তু একটা ব্যাপক জীবনজিজ্ঞাসায় মথিত হয়ে দেকার্তের মতো ঔৎসুক্যের চরমে নিয়ে যাবার মতো ছেলেবেলা আমাদের নেই বললেই চলে। সে ধরনের মানসিক গড়ন, সে ধরনের মানবিক আয়োজন, আমাদের চারপাশে অপ্রতুল। জি এইচ হাবীব ‘সোফির জগৎ’ গ্রন্থখানি অনুবাদ করে আমাদের ছেলেবেলায় মননশীল মানবিক কল্পনার প্রথম সোপান নির্মাণ করলেন। সে নির্মাণ শীর্ষাহরণের জন্যে একটা যোগ্য প্রস্তুতি, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায়।
একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে দর্শনপাঠ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সাধারণের অধিকার লাভের মতোই দুরূহ। কারণ গোড়াতেই এমন কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠে, যার সাথে ঐ বিশেষ বিষয়ের ভাবনার দূরত্ব অনেক। ইয়স্তেন গার্ডার কখনো সোফির মুখ দিয়ে, কখনো অভিনব প্রক্রিয়ায়, কখনো গল্পের ঢঙে সে-সকল সহজ প্রশ্ন থেকে বিশেষ ভাবনার দ্বার পর্যন্ত সেতুবন্ধ তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু সহজ বাঙালির, ১৫-তে পা দেয়া মাটি-কাদায় বেড়ে ওঠা সে-সব কেবল বিস্ময়ের ঘোরলাগা বাঙালি ছেলেমেয়েদের সেখানে প্রবেশাধিকার কোথায়? অনুবাদক সে-সব সহজ ভাবনা থেকে বিশেষ ভাবনায় যাবার সেতুবন্ধের দ্বার উন্মোচন করেই নিস্ক্রিয় হননি, পরমনিষ্ঠায় সুকোমল সে পথখানি বহুযতেœ বুনে গেছেন – যাতে পাঠকের পায়ে কোনো অজানা অন্ধকুঠুরিতে লুকিয়ে থাকা কাচপাকড়ার আঘাত না-লাগে; ঘোরগ্রস্ত পাঠক-পাঠিকা চলতে যেয়ে হোঁচট না খায়। সেজন্য মাঝখানের বহুকষ্ট গিঁটগুলো সহজ-যতেœ খুলে দিয়েছেন। অর্ধেক পথ যেয়ে নিছক নরওয়েজিয়ান কোনো এক মেয়েকে দেয়া দর্শন বিষয়ক কোর্স পড়ছি, এই বোধ দ্বারা যাতে বাঙালি পাঠক-পাঠিকা আক্রান্ত না হন, এ-জন্য আদ্যোপান্ত ভাষার লাবণ্যে, ভাষার বাঙালিয়ানায়, একই বিষয় বারবার এসে গেলে কীভাবে তার মোড় ঘোরাতে হবে তার মুন্সিয়ানায়, বাংলা ‘সোফির জগৎ’ গ্রন্থখানি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। সে ভাষার বাঁধুনি যেমন সংহত তেমন সংযত।
কবিতা, গল্প বা উপন্যাস অনুবাদের ক্ষেত্রে তার প্রধানতম দায় যেমন, কত গভীরভাবে কিংবা কত অকৃত্রিমভাবে তার ভেতরের শিল্পটা ওঠে আসে – তার প্রতি; তেমনি দর্শন বা বিজ্ঞানবিষয়ক অনুবাদে প্রধান দায় বোধ করি পাঠকের প্রতি। পাঠকের বোধগম্যতার প্রতি। কারণ, এমনিতেই এ-সকল বিশেষ বিষয়গুলো সবসময় পরিভাষার ভারে ন্যুব্জ থাকে, তা থেকে তাকে উদ্ধার করে ভেতরের বিষয়টা পাঠকের সামনে মেলে ধরা বা বোধগম্য করে তোলার মধ্যেই সেই পরিশ্রমের স্বার্থকতা। দীর্ঘকাল ধরে দর্শনের উপর বাংলায় লেখা বইগুলো অতি দুর্গমতার অভিযোগে সাধারণ দর্শন পাঠেচ্ছু পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদর পায়নি। প্রথম আমরা স্বার্থক স্বাদ পেলাম সরদার ফজলুল করিমের ‘প্লেটোর সংলাপ’, প্লেটোর ‘রিপাবলিক’, এঙ্গেলসের ‘এন্টিডুরিং’, অ্যারিস্টটলের ‘পলিটিক্স’ – এসকল অসামান্য গ্রন্থের অনুবাদে। শুধু অনুবাদই বলছি কেন রীতিমতো বাঙালিয়ায়ন। সে-সব এক অসাধারণ সৃষ্টি, কোথাও একফোঁটা পাণ্ডিত্যাভিমানে নূয়ে পড়েনি। আগাগোড়াই জীবনের গভীরে বসে জীবনের পরম ভাবনাগুলোর কথা বলে যাওয়া। সে অনুবাদে বিষয়কে গভীরে ধারণ করবার পাশাপাশি, অন্য যে প্রধান বিশেষত্ব ছিল, তা হচ্ছে, পরিভাষাকে অনুবাদ না করে ব্যাখ্যা করা।
কিন্তু ‘সোফির জগৎ’ শুরুতেই একসাথে দুটো বিষয় অনুবাদকের মনোযোগ দাবি করে বসে। এক. তার উপন্যাস ঢঙের অন্তর্নিহিত শিল্প-সুষমা। দুই. তার নিখাদ দর্শন আলোচনা। অনুবাদকের প্রধান পক্ষপাত এবং যথারীতি মুন্সিয়ানা লক্ষ করা যায় ভাষাটাকে আদ্যোপান্ত সরস রাখবার প্রতি, উপন্যাসের রহস্যময়তা কোথাও যাতে টোল না-খায় তার প্রতি। সে-জন্য প্রথম থেকেই যে-ধরনের ভাষার প্রকরণ যার উপর যে-ধরনের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছে, আদ্যোপাšত, গভীর মনোযোগের সাথে তিনি তা বজায় রেখেছেন। সোফির বিরক্তি প্রকাশের ঢঙ বা সোফির বিস্ময় প্রকাশের বৈশিষ্ট্য সাযুজ্যপূর্ণ বাচনে, সোফিকে ১৫ বছরে পা রাখতে যাওয়া, একের পর এক বিস্ময় বিমূঢ় হওয়া, একজন সঙ্গত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। আমরা বুঝতে পারি, হিল্ডা-রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর সোফির প্রকাশ কেমন হবে বা গার্ডেন পার্টিতে তার ঘরোয়া প্রকাশ কেমন হবে। অনুবাদকের হাতে তার অভিব্যক্তির সাজুয্যপূর্ণ প্রকাশ আমাদের মনে তার অখণ্ড মানসিক গড়নের ছবিটা ছাপিয়ে দেয়। এভাবে সময় যত গড়ায় সোফি তত আমাদের হয়। সোফিকে তখন আর সুদূর ইউরোপের আরো দূর নরওয়ের নরওয়েজিয়ান কোনো বালিকা মনে হয় না। সোফি তখন সোফি, আমাদের ঘরের মেয়ে। তার বিস্ময় প্রকাশ, তার মুগ্ধতা, তার বেদনা, বিরক্তি সব যে আমাদের ঘরের প্রকাশ। মেয়েকে নিয়ে তার মায়ের শঙ্কার ভাষা, অ্যালবার্টের পিতৃ-বন্ধু-অভিব্যক্তি – সবকিছুকেই বাঙালিয়ায়ন করেছেন অনুবাদক।
কিন্তু এই গ্রন্থখানি অনুবাদের প্রধান সমস্যা, এই গ্রন্থখানি না-নিখাদ দর্শনের বই, না-নিখাদ উপন্যাস – এক অর্থে দুটোই। যার ফলে উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করতে যেয়ে পরিভাষাগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। আবার পরিভাষা ব্যাখ্যা করতে গেলে উপন্যাস আর উপন্যাস থাকে না। পড়তে পড়তে দর্শন আর উপন্যাসের যৌগ-হাওয়াটা যখনই পরিভাষার ভারে ভারী হয়ে উঠেছে, স্পষ্টতই যা ১৫ বছরের মেয়ের বুদ্ধির অগম্য, তখনই, মনে বেদনা জেগে ওঠে, বাংলাদেশের এই প্রজন্মের কর্মনিষ্ঠ এমন যোগ্য অনুবাদক কী এই সমস্যার সমাধান কল্পে অন্তর্বর্তী কোনো পথ আবিষ্কার করতে পারতেন না?
দেকার্তে যখন বাস্তবতার দ্বৈতধরন বোঝাতে ‘thought’ এবং ‘extension’ শব্দ দুটো ব্যবহার করেছেন, তখন ‘extension’ বোঝাতে ‘ব্যাপ্তি’ শব্দটাই ব্যবহার করতে হবে – এহেন বাধ্যবাধকতায় যেয়ে দেকার্তের দ্বৈতবাদের ভেতরের মজাটা উহ্য করে ফেললেন। ঠিক তেমনিভাবে রোমান্টিসিজম এবং হেগেল অংশে বারবার ‘বিশ্ব চিদাত্মা’ প্রসঙ্গটি এসেছে। ‘চিদাত্মা’ শব্দটি ভারতীয় দর্শনেই এক অস্পষ্ট ধোঁয়াজালে ঢাকা পড়ে আছে। পতঞ্জলি তার যোগ দর্শনে ‘চিদাত্মা’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এক অর্থে, তারপরে ‘চিদাত্মা’ শব্দটির নানা ক্ষেত্র-প্রয়োগ আমাদের বাঙালি মননে একটা ধোাঁয়াটে ভারী বোধ তৈরি করে বসে আছে। এখন এক্ষেত্রে দায় কার প্রতি – সোফির প্রতি? দর্শনের প্রতি? নাকি যথাশব্দের প্রতি?
এভাবেই পারিভাষিক শব্দ এসে সরস সোফির জগৎ অকারণ বা সকারণ গাম্ভীর্যে মাঝে মাঝে ভারী হয়ে উঠেছে। আমরা প্লেটোর অষষবমড়ৎরপধষ ঈধাব-কে এতদিন ‘রূপকল্পের গুহা’ হিসেবে ভেবে এসেছি, ‘পুরাণ’ (গুহা-পুরাণ) কোনো অর্থেই নয়। পৌরাণিক কোনো গল্প থেকে প্লেটো ঐ অসাধারণ গল্পটা বর্ণনা করেননি। তা ছিল কল্পনা থেকে জাত একটা রূপক গল্প। ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে প্লেটো সক্রেটিসের মুখ দিয়ে গল্পটা বলিয়েছিলেন। কিন্তু বারবার অষষবমড়ৎরপধষ ঈধাব এর অনুবাদে ‘গুহা-পুরাণ’ শব্দটির ব্যবহার চোখে লাগে বৈকি। বুদ্ধের বিষবিদ্ধ তীরের গল্পটা গার্ডার থেকে একটু বেরিয়ে এসে ঢেলে বললেই বোধ করি বেশি গ্রহণীয় হতো।
অন্যান্য শিল্পের মতো অনুবাদ শিল্পকেও ভেতরের গভীরে – রসে-ভাবে মিশিয়ে না-নিলে তাকে শুধু বাইরে থেকে ধরবার চেষ্টা করলে, সেটা যে নিছক একটা রূপান্তর কর্মে পরিণত হয়, তা আমরা হালের হঠাৎ-বিখ্যাত বইগুলোর রাতারাতি অনূদিত সংস্করণগুলো পড়তে গেলেই টের পাচ্ছি। কিন্তু সোফির জগতের অনুবাদক তার অন্যান্য অনুবাদগুলোর মতোই এই অনুবাদখানিতে বারবার আমাদের অভিভূত করেছেন, তার এই বহুযতœ রূপান্তর কাজটির বাঙালিয়ায়ন দ্বারা। অনেক ক্ষেত্রে গার্ডারের বিশেষ বিশেষ পক্ষপাতগুলোও আমরা স্বাদুপাঠ্য এই অনুবাদকর্মটির গুণে অবচেতনে ক্ষমা করে দিই । এবং আমাদের বিস্ময়বোধ ভেতরের সমস্ত পুরাতনকে হচকচিয়ে দিয়ে আরো এক বৃহৎ ঔৎসুক্যের দিকে নিয়ে যায়, সে ঔৎসুক্য এক মহামানবিক উত্তরাধিকারের প্রতি ঔৎসুক্য।
৭.
আমাদের জিজ্ঞাসা ও আমাদের উত্তরাধিকার
সঙ্গত প্রশ্ন, যা অনেককাল ধরে মানুষকে ভাবিয়েছে, অনেক আলোচনা-প্রতিআলোচনায়, সময়ে সময়ে ক্লিশে হয়ে উঠেছে গোটা ভাবনাটা, তা হচ্ছে, ব্যবহারিক যে-সব জীবন মানুষকে যাপন করতে হয়, যে-জীবন দুঃখ এবং মৃত্যুর কাছে নতজানু, অন্তর্গত সংশয়ের কাছে বিহ্বল, নানা আত্মবৈপরিত্যে ক্লান্ত, গভীর গোপন অসামান্য জৈবনিক বিস্ময়ে মগ্ন, সর্বোপরি ক্ষুধা-দারিদ্র-প্রেম-কাম-মালিন্য-মহত্বে যে-জীবন সব সময় জৈবনিক মনোযোগ দাবি করে বসে আছে; সে-জীবনে দর্শনের ভূমিকা কোথায়? কোনো দুঃখে বা কোনো সত্যে অতীতের এই ভাবনাসূত্রের সাথে তাকে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে? একজীবন মানুষের এমনিই কেটে যায়। সে-জীবনেও জৈবনিক তাগিদে, গভীরের মগ্নতার গাম্ভীর্যে উঠে আসে জীবনযাপনের দর্শন – তা নিয়েও প্রাজ্ঞজীবন কাটিয়ে দেয়া সম্ভব। তবে কী সেই দায় যার জন্য অতীতের সে-পথ খুঁড়ে খুঁড়ে মোহন গলির সন্ধানে বেরুতে হবে? জীবনের সকল সন্ধ্যা, সকল নির্জনতা, সকল মুখরতা, সকল দিনের সকল আলো, কী মলিন, কী মহৎ, তা কি যথেষ্ট নয় মানুষকে তার মননের ঘাটে, মহত্তে¡র কুলে পৌঁছে দেবার জন্য? তবে কেন মানুষকে চিরকালের এই অমীমাংসিত গোলকধাঁধায় টেনে নিয়ে যাওয়া? আর এতকালের এই সুদীর্ঘ অতিক্রমণ থেকে এতো নিশ্চিত যে, বিশ্বাস দিয়ে সত্যে পৌঁছানো যায় না, যুক্তি দিয়ে সত্যে পৌঁছানো যায় না, সংশয় দিয়ে সত্যে পৌঁছানো যায় না। অন্তত তিন হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের দেয়া এই যুক্তি-প্রতিযুক্তি, এই বিস্ময়-সংশয় – তাই প্রমাণ করে। তবে আর কোন্ পথই-বা বাকি রইলো, যে-পথ দিয়ে সত্যে পৌঁছানোর জন্য আর একবার কোমর বেঁধে যাত্রা শুরু করা যায়? বোধ করি, অবচেতনে সেখানে পৌঁছানোর আকাক্সক্ষা ত্যাগ করাই মহোত্তম। সচেতন যাত্রার উদ্যোগ যদি থাকে, তবে তা দুর্লক্ষ গন্তব্যে না-নিয়ে যাক, সে-পথের দুপাশে লভ্য উপকরণগুলোই-বা কম কীসে? সে-সকল প্রাপ্তিই তো মানবসভ্যতার অšতর্গোপনে কাজ করে, সেই অতীতের কতসব মালিন্য থেকে, কতসব অপমান থেকে, মানবসভ্যতাকে মুক্তি দিয়েছে। এ হচ্ছে সচেতন অভিযাত্রার কথা। তবে, এর বাইরে, আরো একটা সত্য আছে, কোনো ভাবনাই, সঙ্গত কারণে, চিরকাল মানুষকে ভাবিয়ে রাখতে পারে না। তার পেছনে সামাজিক বাহ্য কারণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ; অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ভাবনার গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। তেমনি, আরেকটা কারণও সত্য যে, অপার বিস্ময়, অপার বৈচিত্র্যবোধ মানুষের সহজাত। দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী মন যেমন ক্লান্ত হয়ে যুক্তিতে আশ্রয় খোঁজে, মগ্ন-বিস্ময়ে প্রশ্ন করে বসে – জগতের মৌল উপাদান কী? ঠিক তেমনি, দীর্ঘদিনের যুক্তিক্লান্তমন রোমান্টিসিজমে আশ্রয় খোঁজে, মগ্ন-হাওয়ায় দোল খায়; নাইটিঙলের কণ্ঠ শুনে হ্যামলক মদিরা পানের মতো বুঁদ হয়ে যায় – এই হচ্ছে মানুষের সত্য। সুতরাং দর্শনের এই অভিযাত্রা মানুষকে কোনো সত্য-গšতব্যে না-পৌঁছে দিক, তার যে পার্শ্ব-উৎপাদ, তা থেকে মানুষের মহৎ অর্জন কম নয়। আর এ-তো আমরা জানি, যে সভ্যতা যত তার পেছনটাকে দেখতে পায়, সেই সভ্যতা তত তার সামনে তাকাবার অধিকার লাভ করে।
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেই সুদূর অতীতকালে, এথেন্সের স্বর্ণযুগে জ্ঞান যেমন অখণ্ড একটা বিষয় ছিল, প্লেটোর লাইসিয়ামে শরীরচর্চা থেকে শুরু করে গণিতশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান সবকিছুই আলোচনা হত। এখন, বেলা বাড়ার সাথে সাথে অখণ্ড জ্ঞানের সেই প্রাজ্ঞ বৃক্ষটি হাজারো ডালপালা, লতায়-পাতায় লতিয়ে-গজিয়ে অচিন হয়ে উঠেছে। মানুষের সকল মানবিক ভাবনাই এখন খণ্ডিত। অথচ যা কিছু মানবিক, তার সমস্তই যদি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অধীত না হয়, তবে কোনো জ্ঞানই বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন করতে পারে না।
দীর্ঘকাল ধরে দর্শনশাস্ত্র, দু’একটা বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ ছাড়া, ক্লাসে শিক্ষকের ভারী চশমার নিচে প্রজ্ঞার ছাপ ফেলে-ফেলে এবং নিদ্রালু ছাত্রের মস্তিষ্কে এক জটিল অভিঘাত সৃষ্টি করে অনেক দুর্নাম কুড়িয়েছে। তাকে জীবনের সঙ্গে মাখিয়ে, জীবনের রসে ডুবিয়ে, অতীতের সেইসব ধূপ, গন্ধ দ্রব্যাদিসহ নানা উপকরণ যোগে, আমাদের মহোত্তম অর্জন হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি। নিছক পরিবেশনার গুণেই নয়, বা নিছক গল্পের ঢঙে দর্শন বলার গুণেই নয়, ‘সোফির জগৎ’ অনন্য এ-কারণে যে, মানুষের মধ্যে বসে মানবিক পরম্পরার গল্প বলে গার্ডার আমাদের মানস-ভ্রমণ ঘটাচ্ছেন, সেই সুদূর অতীতের ঈজিয়ান সাগরের কুল থেকে হালের মহাবিস্ফোরণ পর্যন্ত। আমরা গন্ধ পাই এথেন্সের বিষণ্ন সন্ধ্যার, আমরা মগ্ন হয়ে ঢুকে পড়ি – এপিকিউরানদের বাগানে, আমরা দেখতে পাই কীভাবে সেমিটিক জাতিগোষ্ঠী ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে ইন্দো-ইউরোপিয়ান জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভাবনায়। সেই সাথে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের জমিয়ে তোলা মানবিক পরম্পারার এই সিঁড়িগুলো আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে পার হতে থাকি : আশা, ওপারে অপার হবার ইঙ্গিত; আশঙ্কা, কোন্ গোপনে না-জানি কোন্ গভীরে লীন হবার সুর বেজে ওঠে।